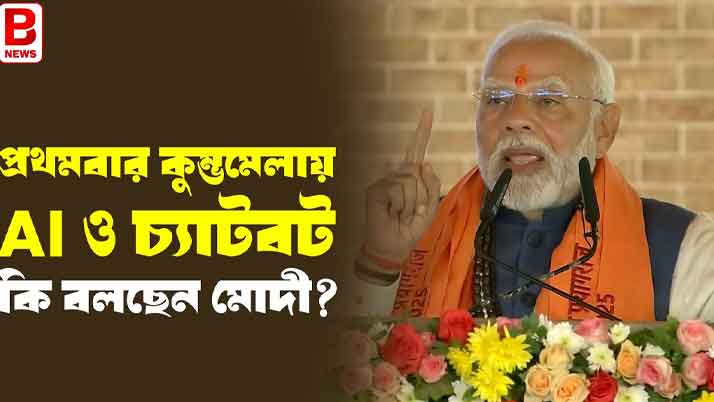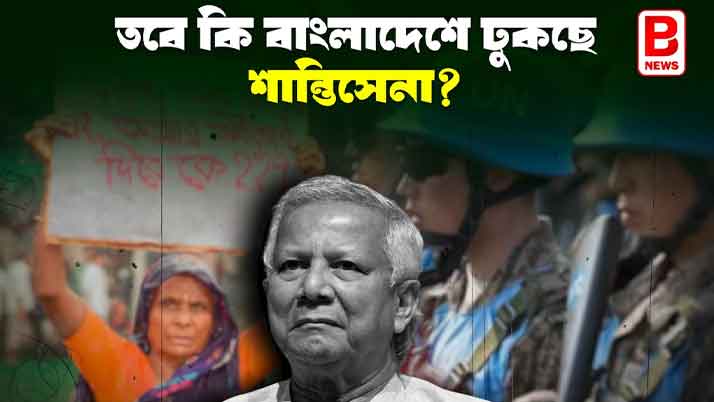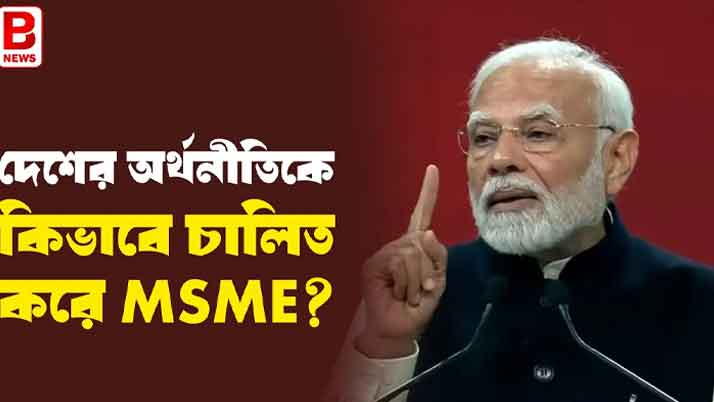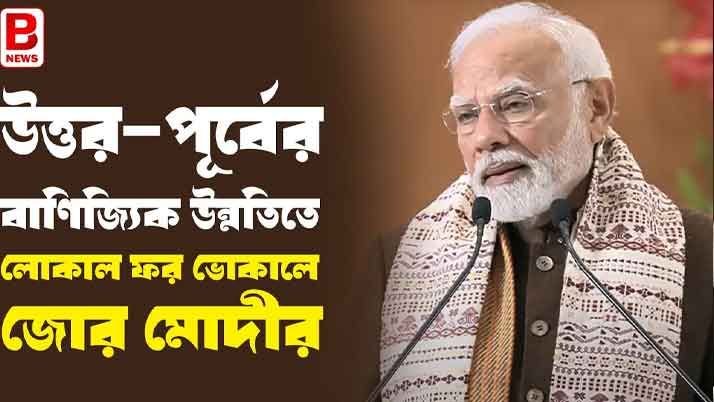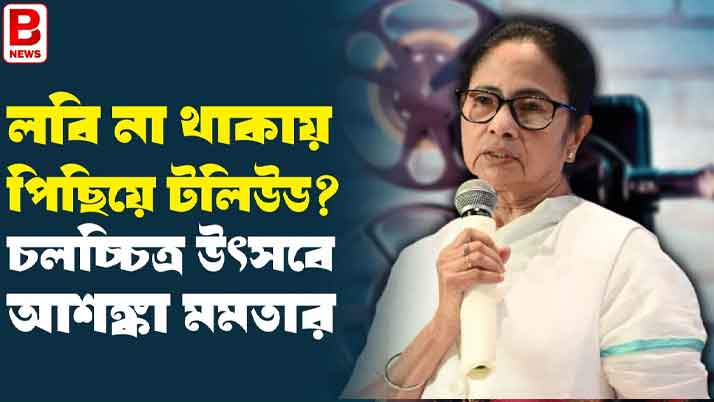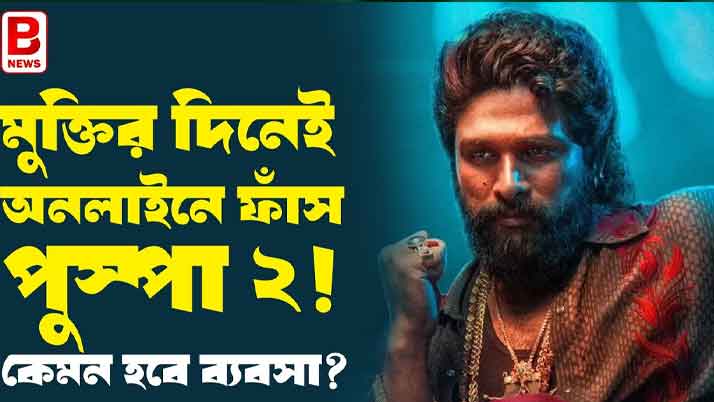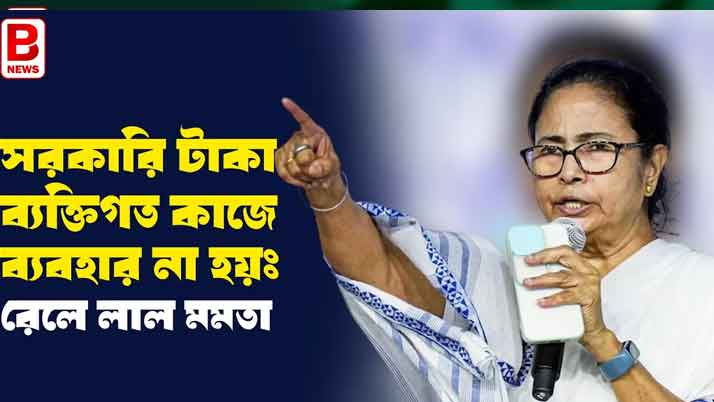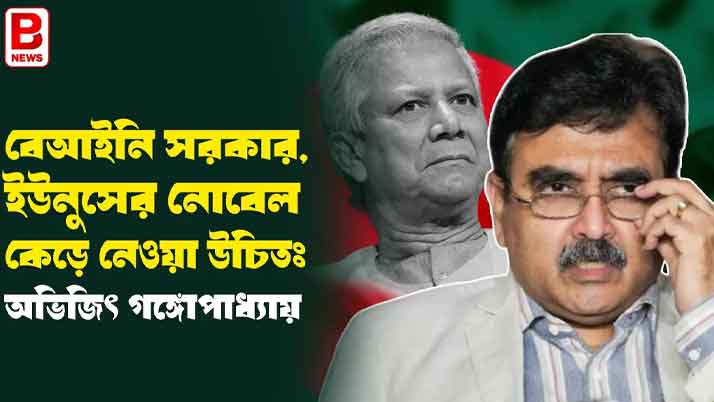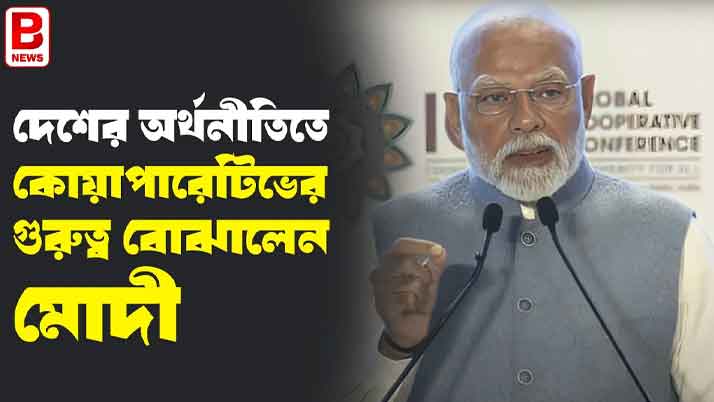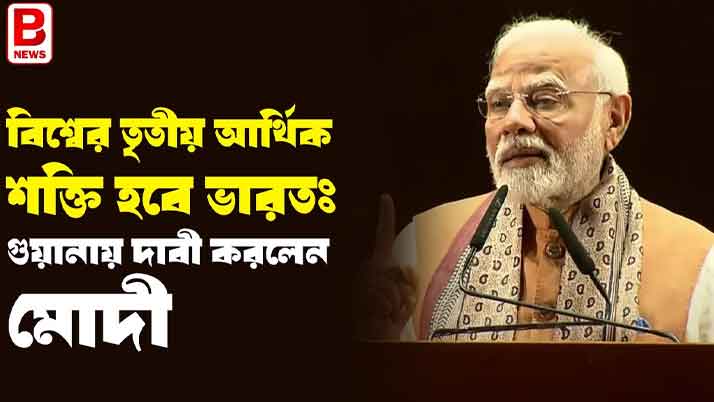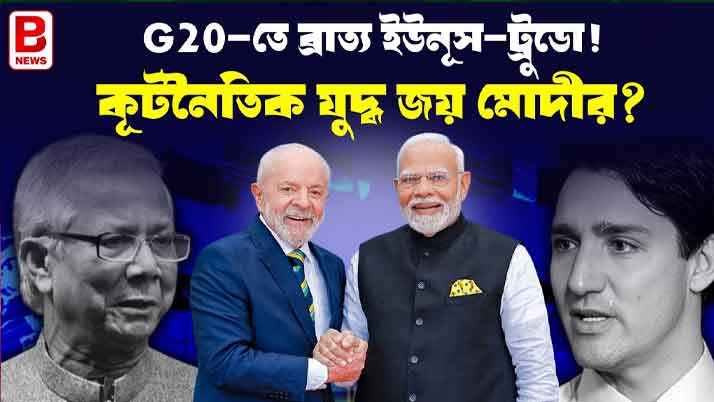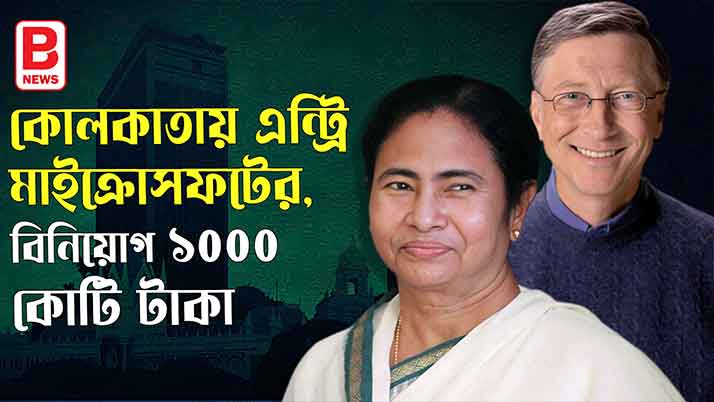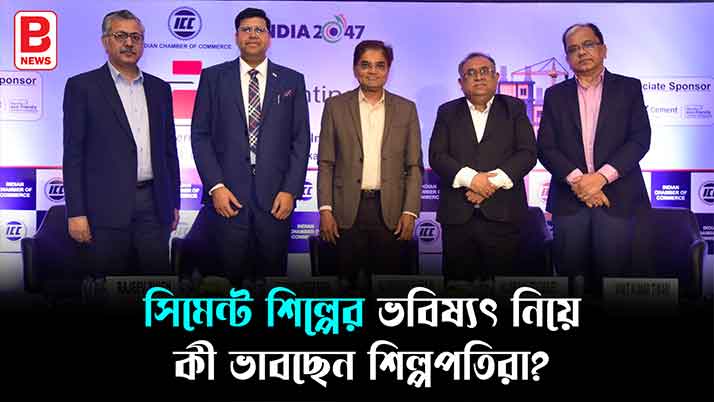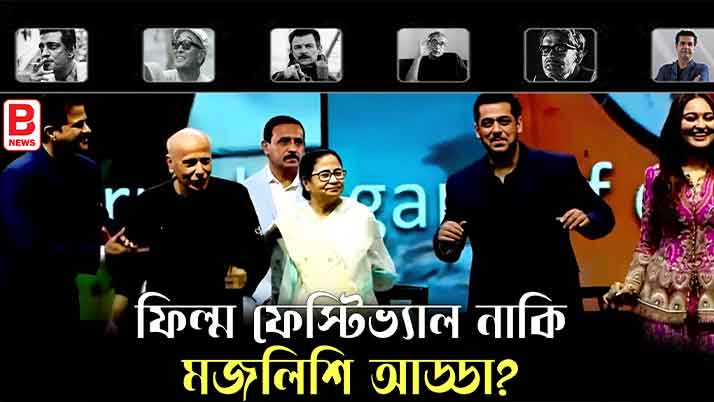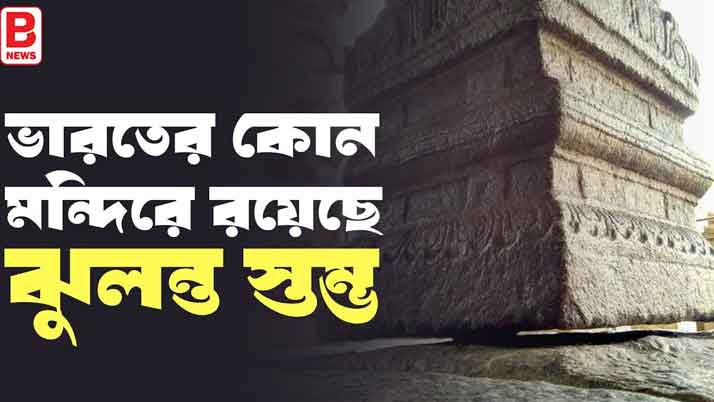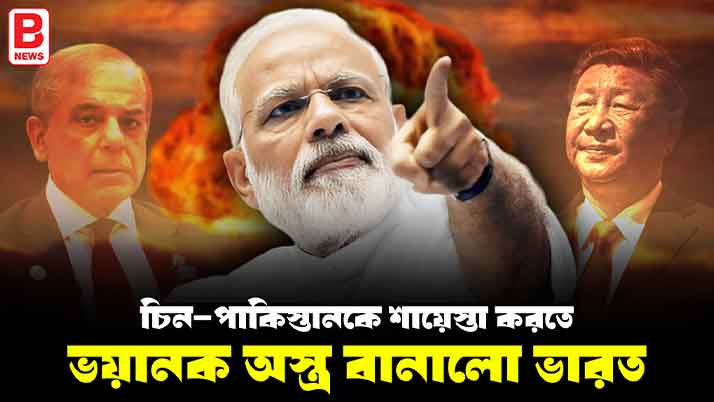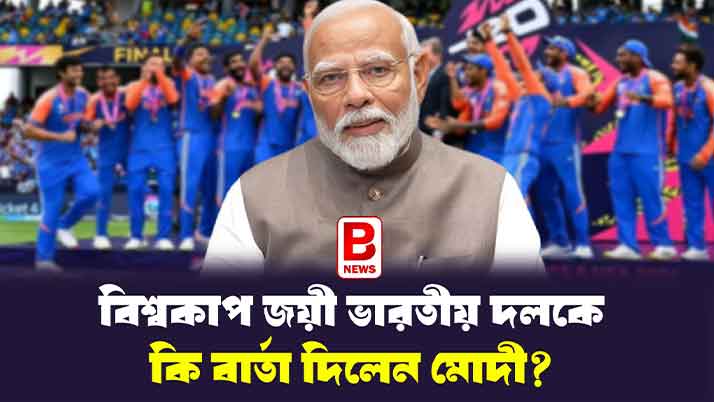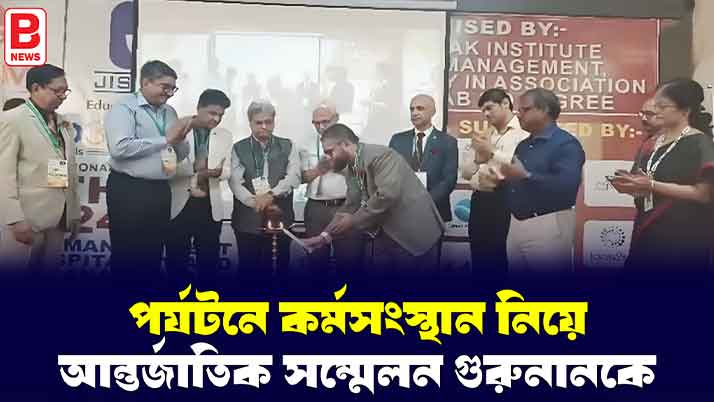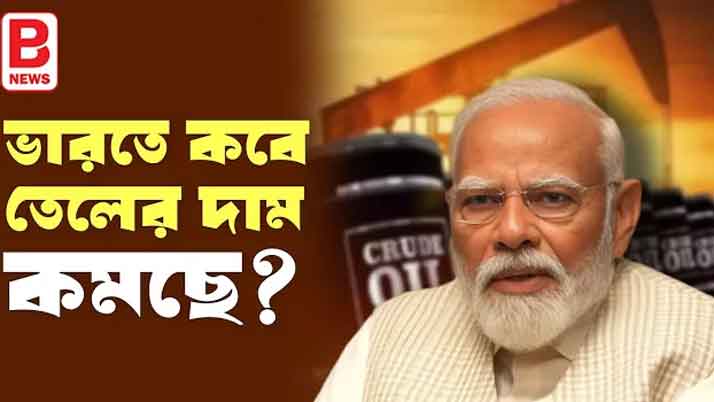Trending
১৯৯০ সালে অর্থনীতির উদারীকরণ ছিল ভারতের জন্য একটা মাস্টারস্ট্রোক। কিন্তু তারপর ইন্ডিয়ান ইকোনমিতে একটা রেভোলিউশন এনে দিয়েছে ইউপিআই বা ইউনিফায়েড পেমেন্ট ইন্টারফেস। আর এই ইউপিআইকেই ধীরে ধীরে ভয় পেতে শুরু করেছে আমেরিকা। কারণ আমেরিকাও বুঝতে পেরেছে যে, অর্থনীতির একচ্ছত্র অধিপতির খেতাব হয়ত এবার খোয়াতে হতে পারে। সেই দায় বর্তাবে বাইডেন প্রশাসনের ওপরেই। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার এই ইনিশিয়েটিভ কিভাবে আমেরিকার ভিসা, মাস্টারকার্ডকে সেয়ানে সেয়ানে টক্কর দিতে চলেছে, এই প্রতিবেদনে সেটাই খোলসা করব একে একে। তার সঙ্গে বলব ইউপিআই-এর ছোট্ট একটা ইতিহাস।
ইউপিআই আসলে কি? এটা একটা পেমেন্ট মেথড। কিন্তু আপনি বলতেই পারেন যে আমাদের আরটিজিএস আছে, এনইএফটি আছে, আইএমপিএস আছে। তাহলে আবার ইউপিআই অকারণে নিয়ে আসা কেন? তাহলে ২০০০ সালে চলে যাওয়া যাক। যে ব্যক্তি ২ লক্ষ টাকার ওপর ট্রানজাকশন করতে চান, তাদের জন্য আরবিআই নিয়ে এলো আরটিজিএস। কিন্তু যদি ২ লাখ টাকার কম ট্রান্সফার করতে হয়? আরবিআই তখন নিয়ে এলো এনইএফটি। কিন্তু দেখা দিল অন্য সমস্যা। কেউ করতে চান ৫ হাজার টাকা, তো কেউ আবার ১০ হাজার টাকা। আরবিআই বলল, ঠিক আছে। তাহলে আধ ঘন্টার গ্যাপে গ্যাপে করতে হবে পেমেন্ট। কিন্তু সাধারণের অসুবিধে হচ্ছিল তখন। কারণ ২ লাখ টাকার কম ট্রানজাকশন করতে হবে এদিকে আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করার মত ধৈর্য মানুষের নেই। অগত্যা ২০০৮ সালে আরবিআই একটা আলাদা অর্গানাইজেশন তৈরি করল। নাম দেওয়া হল এনপিসিআই বা ন্যাশনাল পেমেন্ট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া। এরপর ২০১০ সালে একটা নতুন প্ল্যাটফর্ম এলো। নাম দেওয়া হল আইএমপিএস। এতে একদিকের ঝামেলা তো মিটল। কিন্তু অন্যদিকে? এখনকার মতন কি ১০ টাকা, ১০০ টাকা পেমেন্ট করা তাও আবার যেখানে সেখানে সম্ভব কি হচ্ছিল? এছাড়াও বেনিফিশিয়ারি অ্যাড করার হ্যাপা ছিল। অতএব, প্ল্যাটফর্মটা যেন সরল হইয়াও ঠিক হইল না সরল। সুতরাং এসব ঝামেলা হটাও। পরিবর্তে আরও সোজাসাপ্টা কোন প্ল্যাটফর্ম আনার কথা ভাবল আরবিআই। অবশেষে তারা লঞ্চ করল আইএমপিএসের বেটার ভার্সন। আর এটাই হল ইউপিআই। বলা হয়, ইউপিআই মূলত রঘুরাম রাজনের ব্রেন চাইল্ড। এটায় কি সুবিধে হল? আইএমপিএসের সব সুবিধেই এখানে রইল। বেনিফিট বলতে অ্যাড হল এক ভার্চুয়াল আইডি। যাকে আমরা ইউপিআই আইডি হিসেবেই জানি। এখন এই ইউপিআই আইডির মাধ্যমেই যে কাউকে পেমেন্ট করা সম্ভব- তাও আবার এক পলকেঃ ২৪ ঘন্টা, যখন তখন। সবথেকে বড় কথা এই পেমেন্ট করার জন্য কোন চার্জ লাগবে না, বিক্রেতার অ্যাকাউন্টেও যে কোন মূল্য ট্রান্সফার হয়ে যেতে পারে। এছাড়া ইন্টার অপারেবিলিটি। মানে যার পেটিএম অ্যাপ আছে তাকে শুধু পেটিএম দিয়েই ট্রান্সফার করার প্রয়োজন নেই। যার জিপে তাকে জিপে দিয়েই পেমেন্ট করতে হবে এমন কোন বাধা রইল না।
২০১৬ সালে লঞ্চ হবার পর এই সব কারণের জন্যই পেমেন্ট করাটা আরও সহজ হয়ে গেল। কিন্তু এমন জনপ্রিয়তা কী করে? ফোনপে বলল, তারা ইউপিআই-এর সঙ্গে অ্যাড হতে চায়। জিও আসার পর যেন আরও বুস্ট পেল ইউপিআই। তারপর ডিমনিটাইজেশন। সুতরাং হাতে নোট নেই, কিন্তু ডিজিটাল পেমেন্ট- সেটাই একমাত্র অপশন হয়ে দাঁড়াল। সরকার এক্ষেত্রে একটা মোক্ষম চাল দিল। সরকার বলল, শুধু আমাদের প্রচারে এটা কতটা সাকসেসফুল হবে জানা নেই। অতএব সব ধরণের সরকারি, বেসরকারি সংস্থার কাছে জিনিসটা ছড়িয়ে দেওয়া হোক। ফোন পে-র পর এলো জিপে। তারপর এলো পেটিএম। ধীরে ধীরে যখন সমস্ত বেসরকারি সংস্থা ইউপিআই-কে মান্যতা দিতে শুরু করল, তখন জনপ্রিয়তা পেতেও আর খুব একটা অসুবিধে হল না।
এখন ইউপিআই আসাতে আমেরিকার ভয় কেন? আমরা সকলেই জানি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক সিস্টেমে দাদাগিরি ধরে রেখেছে আমেরিকা। এছাড়া রয়েছে সুইফট টেকনোলজি, ইন্টারন্যাশনাল পেমেন্টের জন্য। এবার আমেরিকা ভাবছে, ভারত যেখানে এই ধরণের একটা টেকনোলজি নিয়ে এলো, সেটা তো ঐ মার্কিন মুলুকেও নেই। এছাড়াও ভারত সরকার নিয়ে এলো এনপিসিআই। অর্থাৎ শুধু ভারতে নয়। গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে হবে ইউপিআই সিস্টেম। প্রথমে ভুটান, তারপর দুবাই, তারপর সিঙ্গাপুর, তারপর একে একে মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপিন্স, ভিয়েতনামের মতন দেশগুলো রাজি হয়ে গেল। জাপান দেখাল ইন্টারেস্ট। আর সবশেষে দেখাল ফ্রান্স। অর্থাৎ ইউরোপে ইউপিআই সিস্টেমকে ছড়িয়ে দেবার জন্য ফ্রান্স হল প্রবেশদ্বার। আর ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম চালু হলে বছর শেষে লাভবান হবে সরকার নিজেই। এই নোট ছাপানো তারপর মেনটেন করার জন্য সরকারের খরচ হত প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা। সেই খরচটা বেঁচে গেল সরকারের। এবার যাওয়া যাক একটু পিছনে। একটা সময় ছিল যখন আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের কার্ড থাকলে তখন আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের এটিএম ব্যবহার করতে হত। তেমনই এইচডিএফসি এবং অন্যান্য। ভিসা, মাস্টার কার্ড বলল ওসব ঝামেলা সরিয়ে দেওয়া যাক। আমরা এই পুরো সাপোর্ট নিয়ে নিচ্ছি। তার বদলে আমাকে একটু টাকা, পয়সা দিয়ে দিও। এই যে টাকা নিচ্ছে ভিসা বা মাস্টার কার্ড- একেই বলে এমডিআর বা মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট। যা ভ্যারি করে ১-৩% মতন। কিন্তু ইউপিআই-তে এসব চার্জের ঝামেলা তো আর নেই। ফলে ধীরে ধীরে ভিসা, মাস্টারকার্ডের আধিপত্য কমতে শুরু করল। তবে এখানেই শেষ নয়। আরবিআই ইউপিআই-কে নিয়ে আরও বহুদূর যেতে চাইছে। ইউপিআইকে ক্রেডিট কার্ডের সঙ্গে লিঙ্ক করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া রয়েছে ইউপিআই লাইট। মানে ইন্টারনেট ছাড়াই করা যাবে পেমেন্ট। আর সবশেষে লঞ্চ করা হল ইউপিআই ১২৩। এক্ষেত্রে তো পেমেন্ট করার জন্য স্মার্টফোনের প্রয়োজনও রইল না।
বলা হচ্ছে, ইউপিআই যেভাবে নিজের প্রসার গোটা বিশ্বে ছড়াতে চলেছে সেটা ইতিমধ্যেই দেশে-বিদেশে প্রশংসার ঝড় তুলেছে। এখন জানা যাচ্ছে, প্রতিদিন ইউপিআই ২২ কোটি ট্র্যানজাকশন করে। প্রতি মাসে যার গ্রস মার্কেট ভ্যালুয়েশন ১০ লক্ষ কোটি ছাড়িয়ে যায়। আর বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে গেলে দিনের শেষে ভারতই ইকোনমিক ওয়ার্ল্ডে নিজের ক্যারিশ্মা দেখাবে। আপাতত এই ভয়েই কাঁপছে ভিসা, মাস্টারকার্ড।
বিজনেস প্রাইম নিউজ।
জীবন হোক অর্থবহ